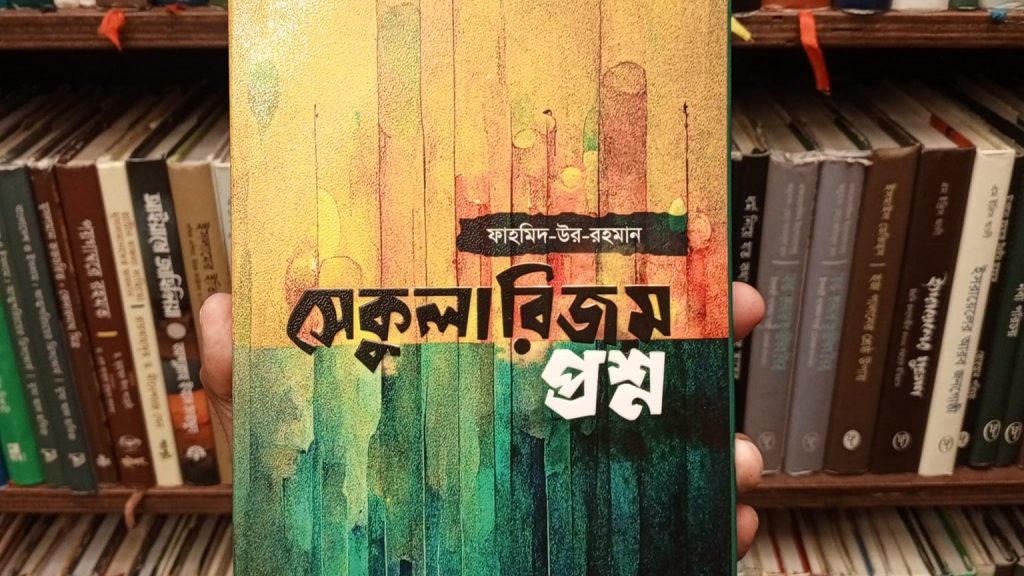
ফাহমিদ-উর-রহমানের সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থ ‘সেকুলারিজম প্রশ্ন’ ইতোমধ্যে সুধীমহলের দৃষ্টি কেড়েছে। পেশায় ডা. হলেও ফাহমিদ-উর-রহমান বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবিতা ও চিন্তার অঙ্গনে আলোচিত এক নাম । মিশেল ফুকো, গ্রামসি, এডওয়ার্ড সাঈদরা বুদ্ধিজীবিতার যে ধরন-ধারণের উল্লেখ করেছেন—জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তিক সততা, শ্রেণীচেতনার উর্ধ্বে বৃহত্তর মানবিক চেতনা লালন, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মোকাবেলায় সদা লড়াইরত এক সাহসী ও দূর্বিনীত সত্তা—ফাহমিদ উর- রহমানের মাঝে এসকল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।
ফাহমিদ-উর-রহমান যেভাবে বিশ্বমানবতার দুর্গতির কথা বলেন, শোষকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তুলে ধরেন তার জুলুমের বয়ান, তেমনি ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদের মোকাবেলায় তিনি সতত সক্রিয়। একইসাথে বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় প্রশ্নে সদা সংগ্রামরত এক লড়াকু বুদ্ধিজীবী। এই জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস-ঐতিহ্য ও চেতনার প্রতিনিধিত্বশীল কন্ঠস্বর তিনি।
দুহাজার বাইশের একেবারে শেষে এসে ‘সেকুলারিজম প্রশ্ন’ (ডিসেম্বর, ২০২২) বইটি প্রকাশিত হওয়াটা দু-কারণে বেশ তাৎপর্যবহ: প্রথমত, একই বছরে বাঙলাদেশের দ্বিধাবিভক্ত সাংস্কৃতিক রাজনীতির অপর কন্ঠস্বর মোহাম্মদ আজমের ‘সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও বাঙলাদেশ’ (ফেব্রুয়ারী, ২০২২) প্রকাশিত হয়েছে। একই বছরে দুই ধারার দুজন প্রধান ব্যাক্তিত্বের সাংস্কৃতিক রাজনীতি নিয়ে আলাপ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বৈকি।
বিশেষত আমাদের জাতীয় জীবনের সংকট নিরূপণে, করণীয় নির্ধারণে এই ধরণের প্রচেষ্টা খুবই আশাজাগানিয়া। উভয় বইই উনিশ-বিশ শতকীয় টেক্সটগুলোকে পর্যালোচনা করেছে, তুলে এনেছে তখনকার সাংস্কৃতিক রাজনীতির ভেতর-বাহির। যদিও দুটো বইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্বিতীয়ত, এটি এমন এক সময় প্রকাশিত হয়েছে, যখন আমাদের সাংস্কৃতিক রাজনীতির দ্বৈরথ জাতীয় জীবনে উৎকটভাবে প্রকাশিত। ধর্ম বনাম প্রগতিশীলতা, ইসলামিজম বনাম সেকুলারিজমের দ্বন্দ্ব একটি বৃহত্তর জাতীয় বিভাজনের সৃষ্টি করছে।
এবার আমরা বইটি সম্পর্কিত মূল আলাপে প্রবেশ করব। তবে প্রবেশের আগে দুটো নোক্তা দিয়ে রাখি।
এক. এই বই পাশ্চিমা সেকুলারিজমের মতাদর্শিক ক্রিটিক নয়, বরং বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্রিয়তায় ‘সেকুলারাইজেশন/ডি-ইসালামাইজেন’ প্রকল্পের একটি অনুসন্ধান ও নির্মোহ পর্যালোচনা।
দুই. বইয়ে এবং এই লেখায় ‘সেকুলার’ ‘সেকুলারিজম’ ‘সেকুলারাইজেশন’ প্রপঞ্চগুলো ডি-ইসলামাইজেশন প্রজেক্টের সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত বাঙলাদেশে ‘সেকুলারিজম’ পরিচয়ধারীদের ইসলামোফোবিক চরিত্র ও এর পেছনে ডি-ইসলামাইজেশনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের একটি সরল সমীক্ষা ‘সেকুলারিজম প্রশ্ন’।
যাইহোক, এবার সরাসরি বইয়ের আলাপে প্রবেশ করা যাক। বইটি মোট পাঁচটি অধ্যয়ে বিভক্ত। ‘সেকুলারিজম প্রশ্ন’ ‘মুসলিম সাহিত্যসমাজ : পূর্ববঙ্গে ইসলামবিদ্বেষের সাংস্কৃতিক পটভূমি’ ও ‘আবদুর রাজ্জাক থেকে আহমদ ছফা : সেকুলারিজমের পালাবদল’ শিরোনামে প্রথম তিন অধ্যায়জুড়ে মূলত সেকুলারাইজেশনের উৎপত্তি ও বিকাশের একটি ইতিবৃত্ত ও পর্যালোচনা উঠে এসেছে। আর ‘হুমায়ুন কবির : আমাদের সেকুলার হয়ে ওঠার বিপদ’ ‘সৈয়দ মুজতবা আলী : জাতীয়তাবাদের দোলাচল’ শিরোনামে শেষ দুটো অধ্যয়ে দুজন মুসলিম প্রতিভার ‘সেকুলার’ হয়ে ওঠার ‘বিপদ’ ও তাদের মেধার বিপুল অপচয়ের খাতিয়ান উঠে এসেছে। প্রথম তিন অধ্যায় সামনে রেখে আজ আমরা বাঙলাদেশে সেকুলারাইজেশনের সিলসিলা তুলে ধরবো।
পটভূমি :
বাঙলাদেশে সেকুলারিজম প্রবেশের আলোচনার আগে উনিশ ও বিশ শতকের রাজনীতি-অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে হবে, যা আমাদেরকে এদেশে সেকুলারিজম প্রবেশের পটভূমি জানতে সহায়তা করবে।
সতেরশ সাতান্নর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে এক সুদূর পরাজয় ও স্থায়ী ক্ষতির আবর্তে পতিত হয়। সদ্যক্ষমতাহারানো শোকবিহ্বল মোসলমানেরা ঔপনিবেশিক শাসনের কোনরূপ সুবিধাভোগী তো হয়নি, বরং তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা ও সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করে। অপরদিকে হিন্দুরা বৃটিশরাজের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সুযোগসুবিধা ভোগী হয়। এভাবে বৃটিশ রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হয় যাদের হাত ধরে ক্রমে এখানে হিন্দু সমাজে একটি রেনেসাঁস হয়, যা বেঙ্গল রেনেসাঁ হিসেবে পরিচিত। তথাকথিত এই রেনেসাঁস উনিশ শতকের সবচেয়ে বিতর্কিত একটি অধ্যায়।
এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য হলো—(ক) এখানকার তৈরি বাঙালিত্বের সংজ্ঞায় বাঙালি মুসলমানের অংশীদারত্ব ছিলো না; (খ) কোলকাতায় উৎপাদিত বাঙালিত্ব মুসলিম আত্মপরিচয় ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে তাদের বয়ানে মুসলমানিত্ব ও বাঙালিত্ব পরস্পরবিরোধী দুটো প্রপঞ্চ হিসেবে হাজির হয়। (গ) কলোনাইজারের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় গড়ে ওঠা এই রেনেসাঁ পরিকল্পিতভাবে বাঙালি মুসলমানকে কোনঠাসা ও প্রান্ত্যজ করে রেখেছে। উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যই বেঙ্গল রেনেসাঁর উৎকট বর্ণবাদী ও ইসলামবিদ্বেষী চরিত্রের প্রকাশক; (ঘ) এই রেনেসাঁর হর্তাকর্তারা জমিদারী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের উপর চরম শোষণমূলক আচরণ করে; যা বেঙ্গল রেনেসাঁর যুগপৎ সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে চিত্রিত করে।
এই ইঙ্গ-মার্কিন প্রকল্পের ফলশ্রুতিতে বাঙালি মুসলমান যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক পশ্চাদপদতার স্বীকার হয়, তার উত্তোরণকল্পে এখানকার রাজনৈতিক নেতাদের দাবী ছিলো— ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববাংলাকে স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হোক; যাতে এই রাজধানীকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র প্রদেশে সরকারি সুযোগ-সুবিধাসমেত বাঙালি মুসলমান তার অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক পিছুটান কাটিয়ে উঠতে পারে। স্বভাবতই এই দাবী ছিলো বেঙ্গল রেনেসাঁর বরকন্দাজদের জন্য ‘হুমকি’। কারণ এই দাবী বাস্তবায়িত হলে তাদের একাধিপত্য ও শোষণনীতি চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হবে।
ফলে বৃটিশরাজ পূর্ববাঙলাকে ১৯০৫ সালে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়ায় তারা চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। পূর্ববাঙলার স্বাতন্ত্র্যকে ‘বঙ্গভঙ্গ’ নাম দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের নামে ‘বঙ্গভঙ্গ‘ রদের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের চাপে বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয় বটে, তবে মুসলমানদের এই হতাশার উপশমকল্পে বাঙলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে ইতিহাসের কলঙ্ক এটাও যে, বেঙ্গল রেনেসাঁর সন্তানেরা পূর্ববঙ্গের এই বিশ্ববিদ্যালয়ও মেনে নিতে পারছিল না। চরম বর্নবাদিতা, জাত্যাভিমান, ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়ে এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তবে শেষতক ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠী তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে নিজেদের পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখতে থাকে।
প্রশ্ন হতে পারে বাঙলাদেশে সেকুলারিজমের পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে কোলকাতার বেঙ্গল রেনেসাঁ, বা পূর্ববাঙলায় প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ কেন আসছে? ‘বেঙ্গল-রেনেসাঁ’ বা ‘ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের’ সঙ্গে এখানকার সেকুলারাইজেশনের সম্পর্কই বা কী?
হ্যাঁ, এখন এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজবো আমরা। ফাহমিদ-উর-রহমানের অনুসন্ধানে বাংলাদেশে সেকুলারিজমের উৎসমুখ চিহ্নিত করতে গেলেই এর জবাব মিলবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সেকুলারিজমের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠা বা বাঙালি-মুসলমানের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা
পূর্বের আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে মুসলমাদের স্বপ্নের কথা আলোচিত হয়েছে; বলা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বেঙ্গল রেনেসাঁর সন্তানদের বিশ্বিবদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে নস্যাৎ-প্রচেষ্টা ব্যার্থ হবার কথাও। মূলত রেনেসাঁর ধ্বজাধারী এইসকল বাবু হিন্দুরা তাদের জমিদারি হারানো ও সাংস্কৃতিক একাধিপত্য খর্বের এই ধাক্কা মেনে নিতে পারছিল না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নতুন পরিকল্পনা আটলো। বইয়ের পাঠ—” ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত পিছিয়ে পড়া পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ব্রাহ্মণরা এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এদের বিরোধিতার মুখে মুসলিম নেতারা অনেক লড়াই করে এ বিশ্ববিদ্যালয় শেষমেশ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।
এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর মতো নেতারা চেয়েছিলেন এটি মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হবে এবং বাঙালি মুসলমান তরুণরা আধুনিক শিক্ষা পেয়ে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্গামিতা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারবে। তারা প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে আলীগড়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড় হতে পারেনি। এর কারণ আমরা এখন একটু খতিয়ে দেখব।
প্রথমদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্ররা ছিল সংখ্যালঘু। অন্তত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অবধি। এর একটা প্রধান কারণ ছিল মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা নেবার মতো যথেষ্ট অর্থনৈতিক সংগতি ছিল না। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টিতে যোগ দেওয়ার মতো বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান শিক্ষক পাওয়া যায়নি। এই শূন্যতার সুযোগ নেয় বাঙালি হিন্দুরা এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল, তারা এসেই এটির ফ্যাকাল্টি ভরে ফেলে।
এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যাত্রা কালেই এখানে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর শিক্ষানৈতিক ও অবকাঠামোগত টুলসগুলো হিন্দুদের হাত দিয়েই তৈরি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বেনিফিশিয়ারি হয় হিন্দুরাই। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে না পারলেও হিন্দুরা এটিকে সাংস্কৃতিকভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডামি বানিয়ে ফেলে। ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে যে মুসলমান ছেলেরা বেরিয়ে আসে তারা মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো আবহাওয়া পায়নি। এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী ও বিপজ্জনক!
এ কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ করে পাকিস্তান হবার পরও এখান থেকে যে বিপুল গ্রাজুয়েট সেকুলার চিন্তা ও কলকাতার আরোপণমূলক সংজ্ঞায়িত বাঙালি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে এলো, তার বীজাঙ্কুর খুঁজতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্মেষকালের গলদ ও বিচ্যুতির মধ্যে। হিন্দু অ্যাকাডেমিশিয়ানদের দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত অপরায়ন ও শিখাগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রাজনীতি এই সেকুলারায়নে যে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।” (১)-৩১,৩২,৩৪
এটিই ছিলো মূলত ঢাবির কোলকাতা-উৎপাদিত বেঙ্গলর রেনেসাঁর সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের পূর্ববঙ্গীয় সংস্করণ, কংগ্রেসের ‘অখন্ড-ভারতীয়’ রাজনৈতিক আদর্শ ও সেকুলারিজম/ ডি-ইসলামাইজেশনের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠার ‘ট্রাজেডি’।
শিখাগোষ্ঠী : পূর্ববঙ্গে ডি-ইসলামাইজেশনের কুশীলব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মাথায় আমরা মুসলিম সাহিত্য সমাজের মতো একটা সংগঠনের উত্থান দেখি। এই সংগঠনের মুখপত্র ‘শিখা’ হয়ে ওঠে এদের চিন্তাধারা ও কর্মসূচির বাহন। শিখাকেন্দ্রীক চিন্তাবলয় যাদের দিয়ে গড়ে উঠেছিলো তারা ‘শিখাগোষ্ঠী’ নামে পরিচিত। এককথায় বললে তৎকালীন পূর্ববাংলা ও পূর্বপাকিস্তান হয়ে আজকের বাঙলাদেশে সেকুলারাইজেশন/ ডি-ইসলামাইজেশনের একক দায় যদি কারো উপর বর্তায় তবে তারা হলো—’শিখাগোষ্ঠী’। ফাহমিদ-উর-রহমান তার বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে শিখাগোষ্ঠী ও এদের প্রচারিত চিন্তাধারার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কথিত প্রগতিশীল আন্দোলন তথা সেকুলারাইজেশনের চরিত্র ও প্রবণতা শনাক্ত করেছেন। তাছাড়া তিনি বাংলাদেশে ইসলামিজম বনাম সেকুলারিজমের বাইনারি রচনা, ধর্ম বনাম প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব, ইসলামবিদ্বেষ ও ইসলামোফোবিয়ার বীজ যে শিখাগোষ্ঠীর হাত দিয়ে বপিত হয়েছে—এই উপসংহারে পৌঁছান অত্যন্ত দলিলসিদ্ধ ও যৌক্তিক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে।
শিখাগোষ্ঠীর চিন্তাগত লিগ্যাসি বর্ণনা করে লেখক দেখান—” এদের প্রধান মোহ ছিল পশ্চিম। আর সেই পশ্চিমের আলো চুয়ে উনিশ শতকের কলকাতায় যে হিন্দুদের জাগরণ ও জোয়ার এসেছিল, সেটি তাদেরকে দ্বিতীয় মোহপাশে জড়িয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে মুসলিম সমাজ ভেঙেচুরে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। তার সৃষ্টিশীলতা স্থবির হয়ে পড়েছিল। এরকম একটা সমাজে জন্মগ্রহণ করে এরা এক গভীর হতাশা ও হীনম্মন্যতায় মজেছিলেন। এর থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য তাই তারা উনিশ শতকের হিন্দু জাগরণকে আদর্শ স্থানীয় হিসেবে গণ্য করে এর আদলে বাঙালি মুসলমান সমাজকে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের গড়নটাই যে আলাদা, এর ধর্মীয়-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি যে ভিন্নতর, সেখানে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের টোটকা এনে বসিয়ে দিলেই যে কোনো হিতকারী ফল ফলবে না, এই কাণ্ডজ্ঞানটুকু তাদের ছিল না” (২)-৩৫।
শিখাগোষ্ঠীর সংস্কার পলিসি যে গলদ ছিল, লেখক তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষ্যে তুলে এনেছেন—”সংস্কার বললেই সেটা সংস্কার ও বিপ্লবী একটা প্রচেষ্টা হয়ে যাবে না, যতক্ষণ না তার সাথে সমাজের একটা আত্মিক যোগ থাকে। এই আত্মিক যোগবিহীন সংস্কার চেষ্টাটাই অনেকটা আরোপণমূলক পদ্ধতিতে এরা চালাতে চেয়েছিলেন। এদের মুখপাত্র শিখা’তে সৃষ্টিধর্মী তেমন কোনো লেখা ছাপা হয়নি। এদের যাবতীয় লেখা ছিল মুসলিম সমাজকে ঘিরে এবং এদের সব ধরনের সৃষ্টিশীলতা ব্যয় হতো মুসলিম সমাজের গলদ চিহ্নিত করতে। এদের কাছে মুসলমান সমাজের সমস্যা ছিল অনগ্রসরতা, পশ্চাদ্বর্তিতা, জ্ঞানচর্চার অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অতীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও সম্মোহন। কথা হলো, এ ধরনের সমস্যা কি মুসলমান সমাজ ছাড়া অন্য কোনো সমাজে হয় না?
হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম, জন্মান্তরবাদ, সতীদাহর মতো বিশ্রী প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে এদের প্রিয় মানুষ রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথও কি খুব বেশি সফল হয়েছেন? এমনকি আজ অবধি? সেই কালে মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করাটা বড়ো একটা বিষয় ছিল। মুসলিম নেতারাও সেইভাবে চিন্তা করেছিলেন। এইসব জরুরি প্রশ্ন এড়িয়ে শিখাগোষ্ঠীর নেতারা বললেন- মুসলমান সমাজ অনগ্রসর, পশ্চাদ্গামী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মে মোহাবিষ্ট। এর কারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে নিহিত। তাই ইসলাম ধর্মের একধরনের সংস্কারের পক্ষে তারা মতামত হাজির করলেন। এমনকি তারা শরিয়তের কিছু অংশ বর্জনের পক্ষেও মত দেন। তাদের মতে, এটা করলেই মুসলিম সমাজ শনৈ শনৈ প্রগতির পথে অগ্রসর হবে।”(৩)-৩৬,৩২
বইয়ে তাদের এইসব ভুল পলিসি, এদেশে ইসলাবিদ্বেষের বীজবপনের বিষয়টি বামপন্থী বুদ্ধিজীবী রঈস উদ্দীন আরিফের ভাষ্যে উঠে আসে—”ব্রিটিশ ভারতের দু শ বছর ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-ইতিহাস-ঐতিহ্যের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে গিয়েছিল, সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আপন ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজই ছিল তৎকালীন বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজ। সে কাজটি কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও সৈয়দ আমীর আলীর মতো বাঙালি মুসলিম মনীষীরা অনেক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু শিখাগোষ্ঠী সেই পথে পা না বাড়িয়ে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে নামলেন কলকাতার অনুকরণে মুসলিম সমাজকে ‘আধুনিক’, ‘প্রগতিশীল’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বানানোর উদ্দেশ্যে।
বলাবাহুল্য, শিখাগোষ্ঠী যে ধারায় বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান, সেটি ছিল এ ভূখণ্ডের দুই শ বছরের সবচেয়ে নিপীড়িত, অবহেলিত, বঞ্চিত, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনায় নবজাগরণ ও শক্তিবৃদ্ধির কাজে পূর্ববর্তী তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তা ও আন্দোলনের বিপরীত ধারা। মূলত সেটি ছিল সে সময়কার ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য চিন্তা ও তার সঙ্গে সমন্বিত কলকাতাকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা ও শিক্ষা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা। এর ফলে বাঙালি মুসলমানদের দু শ বছরের আত্মবিস্মৃতির সংকট আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বাঙালি মুসলমান সমাজ, এমনকি নিম্নবর্ণীয় সনাতন ধর্মীয় সমাজ একদিকে ‘আধুনিকতার’ নামে পাশ্চাত্যের অনুকরণে পুঁজিবাদী বিকৃত সংস্কৃতি, অন্যদিকে কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বর্ণবাদী ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসনের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয় ।… সেই শিখাগোষ্ঠীর ঔরসেই আজ থেকে প্রায় এক শ বছর আগে এ দেশে জন্ম নেয় আধুনিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণি— তার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে প্রবল শক্তি নিয়ে উত্থান ঘটে কথিত ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী’ এবং ‘মৌলবাদ’ বিরোধিতার নামে ইসলামবিদ্বেষী এক বিশাল পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর। এমনকি উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদেরও উৎপত্তি সেখান থেকেই।” (৪) ৩৩
এই অধ্যায়ের পরিধিতে লেখক শিখাগোষ্ঠীর মেন্টর কাজী আব্দুল ওদুদের চিন্তাধার একটা ব্যবচ্ছেদ হাজির করেন। সাথে শিখাগোষ্ঠীর অপরাপর ভাবুক যেমন, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রমুখের ভাবনাজগতের একটা ছবি এঁকেছেন। এদের ব্যাপারে লেখকের মন্তব—”আসলে চৌধুরী ও তার সতীর্থরা (শিখাগোষ্ঠী) মুসলিম মনের গড়ন না বুঝেই এখানে একটা ইউরোপীয় রেনেসাঁ আমদানি করতে চেয়েছিলেন। রেনেসাঁ বা রিফরমেশন যা-ই বলি না কেন, সেটা তো ইতিহাস-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বাদ দিয়ে নয়। ইউরোপেও সেটা হয়নি। অথচ মুসলিম ঐতিহ্য ত্যাগ করে তারা বাঙালি মুসলমানের রেনেসাঁ চেয়েছিলেন। এটা তো একটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব ।… ইসলাম ধর্ম ও ধার্মিকতাকে তাদের কাছে গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, অন্ধ বিশ্বাস, আড়ষ্ট বুদ্ধি, অতীতমুখিতা বলে মনে হয়েছিল। মনে হয় তাদের যত ক্ষোভ ছিল মোল্লা-মৌলভিদের ওপর। তাদের মনে হয়েছিল, এরাই ইসলামকে পিছু টেনে ধরেছে। তাই মধ্যযুগে ইউরোপের চার্চের মতো মোল্লাতন্ত্রকে তারা আক্রমণ করেছিলেন। মুশকিল হচ্ছে, চার্চের মতো ইসলামে মোল্লাতন্ত্রের কোনো জায়গা নেই এবং কখনো ছিল না।”(৫) ৫৫, ৫৭
ইসলামের সাথে এদেশের মানুষের যে শতশত বছরের পরিক্রমায় একটা নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়েছে, তার আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতির শেকড় যে ইসলামের মাঝেই প্রোথিত এই বাস্তববোধটুকু শিখাগোষ্ঠীর কর্ণধারদের ছিলো না। ফলে তাদের সংস্কারের সকল প্রচেষ্টা ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টিতেই শুধু কাজ করেছে, এখানকার জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের বদল আনেনি। লেখক তাদের এসব ধর্মবিরোধী সংস্কারের ফর্দ তৈরি করেছেন—”মুসলিম সাহিত্য সমাজের রথীরা যা চেয়েছিলেন, তার একটা ফিরিস্তি করতে পারি—
- ১. ইসলাম ধর্মকে যুগোপযোগী করা।
- ২. ধর্মের আনুষ্ঠানিক অংশ বাদ দেওয়া (তাদের মতে, এতে ধার্মিকতার সমস্যা হয় না) ।
- ৩. শরিয়তের পরিবর্তন।
- ৪. ধর্মনেতাদের আদেশ অগ্রাহ্য।
- ৫. ইসলামের চেয়ে মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ।
- ৬. গুণেমানে রাসূল (সা.)-কে অতিক্রম করার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণা।
- ৭. রাসূল (সা.)-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে তাঁর মনুষ্যত্বকে উদ্যাপন করা—ইত্যাদি। (৬) ৩৭
লেককের মন্তব্য—”এরকম কর্মসূচি যেকোনো সমাজেই প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে, প্রতিক্রিয়ার জন্ম না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।.. একটি অস্বাভাবিক ক্রিয়ার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই হয়। অথচ মুসলমান সমাজে যখন এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তখন শিখাগোষ্ঠীর লোকজন বা এর অনুরাগীরা একে বললেন প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি । কী আশ্চর্য আত্মপ্রবঞ্চনা।” (৭) ৩৭,৩৮
শিখাগোষ্ঠীর সে সমস্ত প্রস্তাব এই সমাজের সচেতন অংশ পুরোপুরি গ্রহন করেনি ঠিক, কিন্তু এই আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুঁজি করে প্রজন্মের বড় একটা অংশের চিন্তাকে প্রভাবিত ও আক্রান্ত করে। যার প্রতিফলন আমরা দেখি পরবর্তিতে নতুন মোড়কে ষাটের দশকে সেকুলারিজমের বিকাশ ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।
ভাষিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ : সেকুলারিজমের রূপান্তর
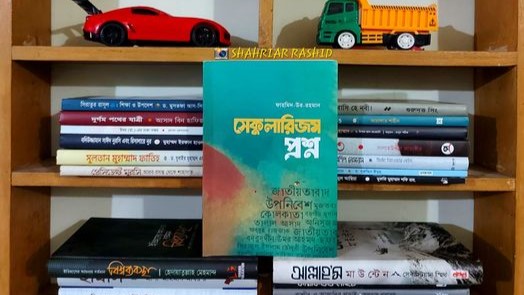
পাকিস্তান হবার পর ষাটের দশকে শিখার পরবর্তী প্রজন্মের সেকুলার ভাবুক ও একশ্রেণির মার্কসবাদীদের হাতে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। এদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, বদরুদ্দীন উমর, আনিসুজ্জামান, আব্দুল হক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ রথী-মহারথীরা। ভাষিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের তত্ত্বায়নে এরা সেইসব যুক্তি ও ভাষাই ব্যাবহার করেছিলেন যা শিখাগোষ্ঠী ব্যাবহার করতো। শিখাগোষ্ঠীর ‘ধর্মবিদ্বেষী’ লিগ্যাসি তারা খুব আয়োজন করেই ধারণ করলো। বইয়ের ভাষ্য—”এদের (শিখাগোষ্ঠীর) যুক্তি ভাষা পেয়ে যায় এ দেশে ভাষা আন্দোলনপরবর্তী ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকট উত্থানের ভেতর। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মডেলটা নেওয়া হয়েছিল কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু রেনেসাঁর শাস থেকে। শিখার মডেলও ছিল হিন্দু রেনেসাঁ।
ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে যে সেকুলার চিন্তার বিকাশ ঘটে, তার পেছনে শিখার যুক্তিগুলোই অনেকখানি কার্যকর ছিল। ১৯৬০-এর দশকে বদরুদ্দীন উমরের লেখা ‘বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন’ এবং ১৯৮০-এর দশকে আহমদ ছফার লেখা ‘বাঙালি মুসলমানের মন’-এ যে যুক্তি সাজিয়ে বাঙালি মুসলমানকে শাপশাপান্ত করা হয়েছে, তার বহু কিছু শিখার চিন্তা থেকে আহরিত। বিশেষ করে এ দুটো লেখার পূর্বসূরি হিসেবে ওদুদের সম্মোহিত মুসলমান– এর কথা বলা যেতে পারে।
ভাষা আন্দোলন পরবর্তী বাঙালি জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে যে বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলা তৈরি হয়েছে, তা শিখারই বিলম্বিত স্বপ্ন পূরণ মাত্র। এই সিলসিলার মধ্যে আছেন আবদুল হক, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ। এদের চিন্তাচর্চার মধ্যে ইসলাম নেই। ইসলামকে কোনোভাবেই এরা আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে মনে করেন না; ইসলামকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতির বিকাশ তো দূরের কথা। আজকে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ভাষা ও ধর্মের ভেতরে লড়াই বাধিয়ে যে রক্তাক্ত বিভাজন তৈরি করা হয়েছে, তার আদি উৎস খুঁজতে হবে শিখার চিন্তাভাবনার মধ্যে ।”(৮) ৫৮,৫৯
বাংলাদেশের পয়দায়েশ, আব্দুর রাজ্জাক ও ছফার রূপান্তর:
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পটভূমি বিচার করতে গিয়ে লেখক বলেন: “বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমিতে এক বিশেষ ধরনের বাঙালি পরিচয় তখন নির্মিত হয়। এই পরিচয় যারা নির্মাণ করেছিলেন, তারা উনিশ শতকে কলকাতার বর্ণহিন্দুদের তৈরি বাঙালি পরিচয়ের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছিলেন। অথচ এই পরিচয় নির্মাণে বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে জড়িত যে মূল জনগোষ্ঠী—বাঙালি মুসলমান, তার ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে আদৌ গণ্য করা হয়নি। উনিশ শতকে কলকাতার বর্ণহিন্দুরা যে সংস্কৃতি তৈরি করেছিল, সেটা ছিল তাদের ওয়ার্ল্ড অর্ডার, মোরাল কোড ও দৈনন্দিন – লাইফ স্টাইলের বাই প্রোডাক্ট । অথচ এই ভিন্ন জাতের সংস্কৃতি দিয়ে একটা মুসলমান প্রধান সমাজকে যখন পরিচিত করার চেষ্টা করানো হলো, তখন থেকেই সংকটটা পাকিয়ে উঠল এবং বাংলাদেশের মানুষের স্বাতন্ত্র্য চিন্তাটা দারুণভাবে বিঘ্নিত হলো। আজকে আমাদের দেশে জাতি পরিচয়গত যে সংকট, তার শুরু এখান থেকেই।” (৯)৬৯
লেখক তৃতীয় অধ্যায়ে ‘আবদুর রাজ্জাক থেকে আহমদ ছফা : সেকুলারিজমের পালাবদল’ শিরোনামে রাজ্জাক ও ছফাকে নিয়ে আলোকপাত করেন। রাজ্জাকের মুসলিম জাতীয়তাবাদী থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠার গল্পের মধ্য দিয়ে তখনকার ক্ষমতা-আকাঙ্খী বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত্বশ্রেণীর ডায়াভার্টের একটা ইঙ্গিত পাবে পাঠক। অধ্যায়ের শেষে আহমদ ছফার মনঃসমীক্ষার পর তার একটি রূপান্তরের আভাস দেন লেখক। তার ভাষ্য—”এটা সত্য যে, ছফা কলকাতার রেনেসাঁর অনুরাগী ছিলেন, এর সৃজনশীলতার মুগ্ধ উপভোগকারী ছিলেন; কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর কালে ছফা তার কলকাতা মুগ্ধতা বাদ দিয়ে কলকাতার সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতাকে পর্যালোচনা শুরু করেন। তিনি একটু একটু করে বুঝতে পারেন; এতদিন আমরা যতই বাঙালি বাঙালি বলে চিৎকার করি না কেন, বাঙালির জগৎ আসলে একটা নয়, দুটো।
‘শরবর্ষের ফেরারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ বইতে তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দেন এবং বাংলাদেশের মুসলমানপ্রধান সমাজের জন্য বাঙালিয়ানা ও সেকুলারিজমের একটি নতুন সংজ্ঞা তৈরির প্রস্তাব দেন। ধর্মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম আগের মতোই চলমান রাখেন বটে, তবে এবার তিনি কলকাতার প্রভাবমুক্ত বাংলাদেশের এক বিশেষ চরিত্রের সেকুলারিজমের ওপর জোর দেন। এভাবে “কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী” থেকে ছফা “বাংলাদেশকেন্দ্রিক সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী”তে পরিণত হন। সম্ভবত ছফার এ পথরেখা ধরেই আমাদের এখানকার বামপন্থি লেখক ফরহাদ মজহার, সলিমুল্লাহ খান ও মোহাম্মদ আজমরা অগ্রসর হচ্ছেন।”(১০)৭৫,৭৬
কোলকাতাকেন্দ্রীক বাঙালি জাতীয়তাবদের বিকল্পে ঢাকাকেন্দ্রীক সেকুলার বাঙালি জাতীবাদের এই রূপান্তরিত চিন্তাই আজকের সেকুলার-চর্চায় প্রতিপত্তিশীল ডিসকোর্স (Dominant Discourse) বলে আমি মনে করি।
সেকুলারিজমের চরিত্র : ইউরোপে ও এখানে
ইউরোপে সৃষ্ট সেকুলারিজমের সাথে এখানকার সেকুলারিজমের চারিত্রিক তফাৎ কী? মিল-অমিল কী? বৈশিষ্ট্য বা সীমাবদ্ধতা কী? তাছাড়া ইউরোপ সেকুলারিজমের সাথে যেভাবে ক্রিটিক্যালি এনগেজড হয়েছে, এখানে তা কতটুকু হয়েছে?
এইসকল গুরুত্বপূর্ণ সওয়ালের একটা সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যাবে বইয়ের বিভিন্ন আলোচনাজুড়ে; যেখানে লেখক ইউরোপের সাপেক্ষে এখানকার সেকুলিজমের চরিত্র ও প্রবণতার নির্মোহ বিচার হাজির করেছেন। লেখকের এসব পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশী সেকুলার ও তাদের সেকুলারিজম-চর্চার ইসলামোফোবিক ও সাম্প্রদায়িক দিকগুলো ফুটে উঠেছে : “আমাদের এখানকার সেকুলারিজমের গতি-প্রকৃতি বুঝতে এদের চিন্তার কাঠামোটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়েছে, এদের চিন্তাভাবনা যতটা না ইউরোকেন্দ্রিক, তার চেয়ে বেশি কলকাতাকেন্দ্রিক ।
ইউরোপে সেকুলারিজমের বিকাশের নানা পর্যায় আছে। এর নানা ওঠানামা ও বাঁকবদলের জায়গা আছে। সেখানে সেকুলারিজম যেমন ধর্মের সাথে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন স্তরে সেকুলারিজমের সাথে ধর্মের বোঝাপড়া ও আপসের জায়গাও আছে। সেখানে সেকুলারিজম ও ধর্মের সম্পর্কটা কোথাও কোথাও বাইনারি হলেও সর্বত্র নয়। এরা কখনো কখনো এক মোহনায় এসে মিলিতও হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সেকুলারিজম সেখানকার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হয়নি। এর পাশাপাশি সেখানকার পণ্ডিতদের সেকুলারিজমের সাথে একধরনের সমালোচনামূলক বোঝাপড়াও আছে। এরা যেমন সেকুলারিজমের ইতিবাচক দিকগুলোর কথা বলেছেন, তেমনি কেউ কেউ এর নেতিবাচক দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। ইউরোপে সেকুলারিজমের সাথে এই যে বিচিত্রভাবে বোঝাপড়া, এটা তাদেরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেকুলারিজমকে সদর্থক অর্থে ব্যবহার করতে সাহায্য করেছে।
কিন্তু আমাদের দেশের সেকুলার ভাবুকদের সেকুলারিজমের সাথে এই ধরনের কোনো ক্রিটিক্যাল এনগেইজমেন্ট নেই। এদের সেকুলারিজম বিষয়ক আলাপ এখনও প্রচলিত প্রগতিশীলতার বয়ানের মধ্যে আটকে আছে। সেকুলারিজমকে বুঝতে ইউরোপে এর বিকাশের বিভিন্ন পর্বগুলো বোঝা দরকার, কারণ এ চিন্তা ওখান থেকেই এসেছে। কিন্তু আমাদের এখানকার সেকুলার ভাবুকদের চিন্তার সীমানাটা কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁর হাত ধরে গড়ে উঠেছে বলে তাদের সেকুলারিজম ব্যাখ্যাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ। এরা সেকুলারিজম বলতে যা লেখেন বা বোঝেন, তা আসলে কতখানি সেকুলারিজম সেটাও একটা পর্যালোচনার বিষয়। এদের সেকুলারিজমের বৈশিষ্ট্যগুলোকে এভাবে শনাক্ত করা যায় :
- . এখানকার সেকুলারিজম বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে চালু হয়েছে।
- . এটা পুরো দম্ভর ইসলামোফোবিক।
- . এখানকার সেকুলারিজম বাংলাভাষীদের মেলায়নি, বিচ্ছিন্ন করেছে মাত্র। এটি কোনো জাতীয় ঐক্যের পূর্বশর্তও তৈরি করেনি।
- . এখানকার সেকুলারিজম প্রগতিশীল নয়; উলটো বহুমাত্রায় সাম্প্রদায়িক। এটা এ দেশের মানুষকে ঠিকমতো প্রতিনিধিত্ব করে না।” (১১) ২৯,৩০
এই সংকট থেকে উত্তোরণকল্পে লেখকের প্রস্তাবনাও সুস্পষ্ট : “সেকুলারিজম তো মানুষের কথা বলে। বাংলাদেশকে যদি একটা জাতিরাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতেই হয়, তাহলে বর্তমানে প্রচলিত সেকুলারিজমের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। এখানকার মানুষ, তার ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস বাদ দিয়ে কোনো সেকুলারিজমের চর্চা স্রেফ পরগাছা সেকুলারিজমে পরিণত হবে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সেকুলারিজম তার বড়ো নজির।”(১২) ৩০
বইয়ের ভালো-মন্দ
‘সেকুলারিজম প্রশ্ন’ বইটি যেই অ্যাপ্রোচে লেখা হয়েছে এই ধারায় সম্ভবত এটি প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র গ্রন্থ। সে হিসেবে এটিকে লেখকের একটি সাহসী উদ্যোগই বলা চলে। বিশেষত আজকের বাঙলাদেশে বুদ্ধিজীবীতার যে একটা রেসিস্ট, সাম্প্রদায়িক ও প্রচন্ডমাত্রায় ইসলামোফোবিক চরিত্রে দেখি—এর উৎপত্তি, ধারবাহিকতা ও সঠিক পর্যালোচনা ইতোপূর্বে হয়নি; ফলে বাঙালি মুসলমানের ভবিষ্যত সাংস্কৃতিক রাজনীতি নির্ধারণে বাঙলাদেশে সেকুলারিজমের অংশগ্রহণ, তৎপরতা ও ইতিহাসকে পুনর্পাঠের এই উদ্যোগকে স্বাগত পাবারই হকদার। সর্বোপরি স্বীকার করছি একটি বিস্তৃত, স্পর্শকাতর এবং একইসাথে জরুরি বিষয়ের বয়ন ও বয়ানে ফাহমিদ-উর-রহমান বেশ সাফল্যের সাথেই উৎরে গেছেন।
অবশ্য এ বইয়ের সীমাবদ্ধতাও আছে দুয়েকটা: যেমন ওদুদ থেকে নিয়ে আহমদ ছফা পর্যন্ত এসে লেখক আর আগাননি। অথচ ছফা-পরবর্তি রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে ইসলামিজম-সেকুলারিজম বাইনারির উৎকট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত শাহবাগে এসে এই উগ্র ভাষিক জাতিবাদী সেকুলার সিলসিলার যে সর্বোচ্চ উত্থান ও প্রকাশ ঘটে, এর কোনো দফারফা লেখক করেননি। শাহবাগের তত্ত্বায়ন কারা করলেন, কারা ফ্যাসিষ্ট রেজিমের আওতায় আরেকটি রেসিস্ট ও ইসলামোফোবিক বিস্ফোরণের জন্ম দিলেন—সে ইতিহাস রচনার জরুরত ও সময় এসে গেছে বৈকি। কাজেই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি লেখক মহোদয় ‘সেকুলারিজম প্রশ্নে’র পরবর্তী সিক্যুয়েলে শাপলা-শাহবাগের সাংস্কৃতিক রাজনীতির জরুরী আলাপ নিয়ে পুনরায় হাজির হবেন।
লেখক: ফাহমিদ-উর-রহমান
প্রকাশনী: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
প্রকাশকাল: ২০ ডিসেম্বর ২০২২
পৃষ্ঠা সংখ্যা: 144
মূল্য: 220 টাকা
